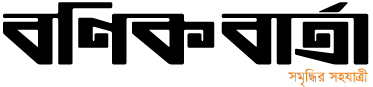ইতিহাস অনেক কথা বলে, যা আমরা অনেক সময়ই দেখতে পাই না। ১৮৪১ সালে চীনের কিং রাজত্বের সময় তাদের হাতে হংকংয়ে বিপুল পরিমাণ এক আফিমের চালান ধরা পড়ে। তাতে চীনের রাজা ঘোষণা দেন, ভবিষ্যতে কেউ তা নিয়ে ধরা পড়লে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। তাতে ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন খুশি হতে পারেন না। তাদের ভাষায়, বাজারের চাহিদা অনুযায়ী, মুক্ত বাণিজ্য এলাকার শর্তানুসারে তাদের এই আফিম বাণিজ্য চলবে। ফলে ইংরেজরা জোর করে হংকং দখল করে নেয় ১৮৪২ সালে। চীনারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে ওঠেনি। এরপর ১৮৫৬ থেকে ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ-ফ্রান্স যৌথ যুদ্ধে হংকংসংলগ্ন কাউ-লুন বন্দর দখল করে নেয়। এ সময়ে চীনে আফিম বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তারা বাংলাদেশে ধানের বদলে আফিম উৎপাদন করে তা সেখানে পাঠাত। ১৮৬০ সালেই ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের যৌথ বাহিনী চীনের রাজাকে চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করে, আর সেই থেকে হংকং ও কাউ-লুনের দখল বজায় থাকে ১৯৯৭ পর্যন্ত। এ সময়ে ব্রিটিশদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র (রাশিয়াও মুখে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিল, তবে সিপাহী পাঠায়নি)। চীনের সঙ্গে ব্রিটিশদের সর্বশেষ চুক্তি হয় ১৯৮৪ সালে, যার মাধ্যমে হংকং চীনের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং ১৯৯৭ সালে তা তারা ফেরত দেয় চীনকে।
১৪৯২ সালে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের সময় থেকেই কিউবা স্পেনের অংশ হয়ে যায়। সেই থেকেই কিউবা ছিল স্প্যানিশ উপনিবেশ। কিউবায় চিনি ও তামাক উৎপাদনের জন্য স্পেন আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসে ক্রীতদাস। এ সময়ে ফ্লোরিডাও ছিল স্পেনের শাসনে। দাস প্রথা চালু থাকা অবস্থায় তাদের ছিল না কোনো জাগতিক অধিকার। পশু ও দাসের মধ্যে ছিল না কোনো ফারাক। আমেরিকার ইতিহাস ও স্বাধীনতা আন্দোলনে ফ্রান্স ও স্পেন যুক্ত ছিল স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে। তাই ১৭৬২ সালে ব্রিটিশরা কিউবার দখল নিয়ে নেয়। অবশ্য ১৭৬৩ সালে ফ্লোরিডার বিনিময়ে ব্রিটিশরা কিউবাকে স্পেনের হাতে ফিরিয়ে দেয়। দাস প্রথার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েই শেষ পর্যন্ত কিউবানদের আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল ১৮২৬ সাল থেকেই। এ সময়ে কিউবা আমেরিকার চিনি চাহিদার প্রায় অর্ধেক মেটাত। অধিকাংশ চিনি ও তামাক উৎপাদনকারী কৃষক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ধনী সাদা কৃষক। ১৮৩৩ সালে ইউরোপে দাস প্রথা রহিত হওয়ার পর অধিকাংশ কিউবার চিনি ও তামাক উৎপাদনকারী কৃষক চাইছিলেন কিউবা যেন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হয়ে যায়। কারণ যুক্তরাষ্ট্রে তখনও দাস প্রথা চালু ছিল। পরে উনিশ শতকের শেষের দিকে স্প্যানিশ-আমেরিকার যুদ্ধের পর ১৮৯৮ সালে তার দখল নেয় যুক্তরাষ্ট্র, কিন্তু ১৯০২ সালেই কিউবা স্বাধীনতা লাভ করে। বুঝতেই পারছেন কীভাবে বিশ্বের শক্তিশালী রাজ্যগুলো নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে অন্যায় কাজ করতে দ্বিধা করে না। স্বাধীনতার পর কিন্তু কিউবা শান্তিতে থাকতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্রের রোষ তাদের ওপর ছিল সর্বদা। কিছুদিন পর পরই চেষ্টা করত সামরিক সহায়তা দিয়ে কিউবায় নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। তাদের সহায়তায় ছিল ব্রিটিশ রাজ, যারা ক্যারিবিয়ান বহুদ্বীপ শাসক করছিল। কিউবায় তখন পীতজ্বর বা ইয়েলো ফিভার, কলেরা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, গুটিবসন্ত প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির ব্যাপক প্রকোপ। প্রতি বছর মারা যেত লাখ লাখ লোক। এরই মাঝে ১৯৫৯ সালে ক্ষমতায় আসেন কাস্ত্রো। প্রায় ৬০ বছরের তথাকথিত ‘স্বাধীনতা’ এবং যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণে কাস্ত্রোর মিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। শুরু হয় ১৯৬০ সালের বিখ্যাত ‘কিউবা সংকট’। সংকটের মাঝে মার্কিনি কৃষকরা ত্যাগ করেন কিউবা। সঙ্গে চলে যায় তাদের পেয়াদারা। একসঙ্গে ডাক্তারের সংখ্যা হয়ে যায় অর্ধেক। বুঝতেই পারছেন, ডাক্তারদের দেশত্যাগে কিউবা হয়ে যায় অসহায়। তখন (ডা.) চে গুয়েভারার দেয়া পরিকল্পনা দিয়ে কাস্ত্রো কিউবার নতুন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন।
গল্প দুটো বললাম কারণ আমাদের মধ্যে যারা মনে করেন যে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ বিপদে আমাদের সহায়তায় এগিয়ে আসবে, তাদের জন্য ইতিহাসচর্চার প্রয়োজন রয়েছে। স্বার্থহীন সহায়তা প্রায় অসম্ভব। আবার আমাদের এই বিপদে (করোনা সংকটের কথা বলছি) যদি ভাবেন অন্য কোনো দেশ ওষুধ দিয়ে উদ্ধার করবে, তাহলেও বলব এটা স্থূলবুদ্ধির প্রকাশ। এ-যাবৎ আমরা কেবল প্রচলিত ওষুধ উৎপাদন দেশে করতে পেরেছি, কারণ তা উৎপাদনের অধিকার আমাদের হাতে আছে, কিন্তু নতুন কোনো ওষুধ সহজে আসবে না। কারণ মেধাস্বত্ব আইন অনুসারে তা আনতে হবে। অবশ্য সদ্য সমাপ্ত ডব্লিউএইচওর সম্মেলনে চীন ও ইউরোপ অঙ্গীকার করে বলেছে যে করোনার জন্য আবিষ্কৃত যেকোনো ওষুধ তারা নিঃশর্তে সারা পৃথিবীকে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। বিষয়টি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তারা দিয়েছে ডব্লিউএইচওকে। দেখা যাবে বাস্তবে তা কী হয়! হংকংয়ের ইতিহাস আমাদের বলে পশ্চিমা বিশ্ব ব্যবসার খাতিরে (আফিম ব্যবসার জন্য) সব অন্যায়কে ন্যায় বলে চালাতেও পারে।
করোনার এ-যাবৎ প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে করোনায় মাথাপিছু মৃত্যুর হার এশিয়ায় সবচেয়ে কম। ইউরোপ কিংবা আমেরিকা যারা জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিত্ত-প্রতিপত্তি কিংবা স্বাস্থ্য খাতে পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নত, তাদের মাথাপিছু মৃত্যু অনেক গুণ বেশি। মাথাপিছু মৃত্যুর হারে বেলজিয়াম, সুইডেন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, জার্মানির ধারেকাছে কেউ নেই। বিত্ত-বৈভবে ভরা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় (ইরানসহ) মৃত্যুহার এশিয়ার অন্য দেশগুলোর চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। গরিবদের মধ্যে রয়েছে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশগুলো, কিন্তু মৃত্যুর মিছিলে তারাও এগিয়ে। আফ্রিকায় সবচেয়ে শেষে করোনা আবির্ভূত হয়েছে তাই এখনো মৃত্যু বেশি নয়, তবে ডব্লিউএইচও এরই মধ্যে বলেছে, আফ্রিকায় মৃত্যুর হার বাড়বে অতিদ্রুত। সবার কাছেই আশ্চর্য এশিয়ার সাফল্য। এশিয়ায় দক্ষিণ এশিয়াকে বাদ দিলে পূর্ব এশিয়ায় মৃত্যুর হার আশ্চর্যজনকভাবে কম। কী কারণ? তা নিয়ে রীতিমতো পিএইচডি করার প্রতিযোগিতা চলছে পশ্চিমা বিশ্বে। মুখ ফুটে বলতে পারছে না, তবে সবাই অবাক! এ সাফল্যের পেছনে ওষুধ বা হাসপাতাল নয়। এর অগ্রভাগে রয়েছে তাদের জনগণ ও সমাজ।
চীনে যেখানে প্রথম এসেছিল, সেখানেও মাথাপিছু মৃত্যুহার বেশি নয়। জাপান, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া সর্বত্রই আক্রান্ত ও মৃত্যু দুটোরই হার কম। কী করে সম্ভব হলো? ওষুধ দিয়ে? তা নয়। ভেন্টিলেটর দিয়ে? তাও নয়। ছোঁয়াচে রোগের প্রধান শত্রু হলো জনগণের আচরণ ও সমাজ। এ দেশগুলো জয় করেছে এই সহজ ও সস্তা পদ্ধতির মাধ্যমে। অবশ্য আক্রান্ত হলে প্রয়োজন হবে ডাক্তার আর ওষুধের। তবে মূল ধারণা হলো, কী করে কম লোক আক্রান্ত হয়, তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে অনেকেই করেছে প্রযুক্তির ব্যবহার।
অনেকের মতে, যে জাতি জনগণকে সঠিক সাধারণ স্বাস্থ্য জ্ঞান দিয়েছে, আর যে জনগণ তা পালন করেছে, সেই দেশই স্বগর্ভে করোনামুক্ত হয়েছে। কী সেই স্বাস্থ্য জ্ঞান? ছোঁয়াচে রোগের ক্ষেত্রে এর উপাদান তিনটি। প্রথমত, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যচর্চা। নিজেকে ও নিজের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা। কীভাবে করবেন? শুধু হাত ধোবেন ঘন ঘন? তা নয়, থাকবেন স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে। স্বাস্থ্যসম্মত মানে দামি পরিবেশ নয়। পরিষ্কার পরিবেশ। বাড়িতে এসে হাত ধোবেন। বাড়ির ভেতরে বাইরের কাপড় ব্যবহার করবেন না। জুতা ঘরে আনবেন না। বাড়ির মেঝে, দরজার ভেতর ও বাইরের অংশ পরিষ্কার করবেন দিনে অন্তত কয়েকবার। এশিয়ার অনেক দেশের সংস্কৃতিতে তা গ্রথিত ছিল বহুকাল ধরে। যে সমাজে এই সাধারণ নিয়ম এখনো চালু ছিল, তাদের মাঝে আক্রান্তের হার কম। আমাদের মধ্যেই রয়েছে উদাহরণ। আমরা অনেক রোগকে এভাবেই জয় করেছি।
বলছিলাম কিউবার কথা। ডাক্তারের অভাবে কিংবা হাসপাতালের অভাবে কিউবানরা কি অধিক হারে মৃত্যুবরণ করেছিল? তা নয়। কি ছিল চে গুয়েভারার মন্ত্রে? তার উপদেশ ছিল, কমিউনিটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। যার মূলে ছিল সাধারণ স্বাস্থ্য সেবক-সেবিকা প্রথা চালু করা। ফলে ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ সাল—মাত্র তিন বছরের মধ্যে কাস্ত্রোর সরকার সারা দেশে সাধারণ স্বাস্থ্যকর্মী দিয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল। পেরেছিল তাদের আচরণগত পরিবর্তন আনতে। প্রায় সব রোগকে তারা জয় করেছিল। প্রতি ২৫ হাজার কিউবানের জন্য তৈরি করেছিল স্বাস্থ্যকেন্দ্র। যাদের দায়িত্ব ছিল প্রতিটি পাড়ায় জনগণের কাছে সাধারণ স্বাস্থ্য শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়া। ফলাফল হয়েছিল ম্যাজিকের মতো।
দ্বিতীয়ত, সামাজিক স্বাস্থ্যচর্চা। নিশ্চিত করা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সামাজিক পরিবেশ। সড়ক-মহাসড়কে আবর্জনা না ফেলা, যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলে না রাখা, সব সামাজিক মিলনকেন্দ্র যেমন হাটবাজার, মসজিদ-মন্দির, স্কুল-কলেজ, স্টেশন-বন্দর, বাস-ট্রেন, এমনকি অফিস-আদালতকে ঝকঝকে রাখা। কেবল স্থানটি নয়, প্রয়োজন শৌচাগারগুলোকেও সমানভাবে পরিষ্কার রাখা। ম্যাজিকের মতো কাজ করবে এ ব্যবস্থা। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাতে আমাদের মনোযোগ নেই। মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়েও আমরা আশা করছি মেয়র আমাদের বাড়িতে এসে তা পরিষ্কার করে দেবেন! আমাদের মনোযোগ অর্থব্যয়ের দিকে। যেন সবাই লোপাটের সুযোগ খুঁজছে।
তৃতীয়ত, সাংস্কৃতিক পরিবেশ—কীভাবে আমরা একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হব। কী করে রাস্তায় চলাচল করব। কী করে দূরত্ব বজায় রাখব। সংস্কৃতিগতভাবে আমাদের সুবিধা অনেক। আমরা অনেকেই ঘরে বাইরের জুতো আনি না। আমি মনেও করতে পারি না যে কজনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছি গত এক বছরে। এটা আমাদের সংস্কৃতির অংশ নয়। দূর থেকে প্রণাম বা সালাম দেয়াই আমাদের রীতি। আমরা রাস্তাঘাটে হাত ধরাধরি কিংবা গলা জড়িয়ে চলি না। সংস্কৃতির সব কিছুই আমাদের পক্ষে (শুধু জানি না কী করে লাইন করে দাঁড়াব! লাইনে দাঁড়ানো আমাদের সংস্কৃতিতে ছিল না বলেই কি তা আমরা করি না!)। বছরে কেবল দুবার আমরা কোলাকুলি করি, তাও মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতির প্রভাবে। মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিমা সমাজে তাই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনতে হবে। তাদের নতুন করে প্রচেষ্টা নিতে হবে কী করে তা করা যায়। এশিয়ার অনেক দেশই এই আচরণের সুবিধা পেয়েছে। যে কয়টি এশিয়া দেশে এই আচরণগুলো গ্রথিত ছিল, তাদেরই আক্রান্তের হার অনেক কম। বাংলাদেশে করোনার প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের মধ্যেও সংক্রমণ কম ছিল। কারণ আমরা ঘরে বসে ছিলাম। (যদিও অনেকে বলবেন টেস্ট না হওয়ায় তা কম তা নয়, রোগের উপসর্গ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই লোকজন পরীক্ষার জন্য রাতভর লাইনে দাঁড়িয়েছে)। তবে এখন যখন অর্থনীতির কর্মকাণ্ড ধীরে ধীরে খুলতে থাকবে, তখন আমাদের প্রয়োজন বাকি আচরণগুলো রপ্ত করা।
কীভাবে সম্ভব? প্রথমটি করবেন আমাদের বিরাট শক্তি এনজিও এবং তাদের কর্মীদের মাধ্যমে। তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমেই বাংলাদেশ সামাজিক সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে ভালো অবস্থান তৈরি করেছে। তারা তা করতে পেরেছিল, কারণ বিদেশীদের সাহায্যে তারা তৈরি করেছে তৃণমূল পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি ও চালু করেছিল তাদের কার্যক্রম। সরকারের উচিত তাদের দিয়েই জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যক্রমকে উপস্থাপন করা। তবে এবার বিদেশী সাহায্যে নয়, দেশীয় অর্থে। প্রয়োজন আগামী বাজেটে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যক্রমকে বাড়ি বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক বরাদ্দ এবং সেই সঙ্গে এনজিওদের সঙ্গে সরকারের অংশীদারিত্ব। পৃথিবীর অনেক দেশেই তা সম্ভব হবে না, কারণ এমন জনবল ও প্রতিষ্ঠান অনেক দেশেরই নেই।
দ্বিতীয়টির জন্য প্রয়োজন সামাজিক পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়বদ্ধতার নিয়ম তৈরি করা। সঙ্গে প্রয়োজন কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য সরকারি বরাদ্দ। হাটবাজার, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট, মসজিদ-মন্দির, অফিস-আদালত, বাস-ট্রেন সব ক্ষেত্রেই রয়েছে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। দেখবেন নানা জায়গায় আদেশ-উপদেশসংবলিত নির্দেশাবলি ঝোলানো আছে। বলা হয়েছে, ‘কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে’। সেই সব আড়ালে থাকা কর্তৃপক্ষকে সরকার দায়বদ্ধ করবে, দেবে আংশিক অর্থ বরাদ্দ আর আনবে জবাবদিহিতার আওতায়। তাদের কাজ হবে স্ব-স্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা। তাদের নিজেদের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। আরো রয়েছে নাগরিক কর্তৃপক্ষ—পৌরসভা, সিটি করপোরেশন—তাদের দায়িত্ব হবে নগরীতে রাস্তাঘাট থেকে ময়লা দূর করা। নগরে প্রতি কিলোমিটার (জনঘনত্ব অনুযায়ী কম-বেশি হতে পারে) দূরত্বে পানি ও শৌচাগার নির্মাণ করা এবং তা চালু রাখা।
তৃতীয়টি আমাদের সংস্কৃতিতে এরই মধ্যে চালু আছে।
বলে রাখা ভালো যে উপরের ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে আমি বলছি না যে আমাদের হাসপাতাল লাগবে না, ডাক্তার লাগবে না, ওষুধ লাগবে না। সংক্রমণ কমলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় চাপ কমবে। করোনায় এটিই এশিয়ার ঈর্ষণীয় সাফল্য।
দেখবেন ম্যাজিকের মতোই অন্য সব পূর্ব-এশীয় দেশের মতো আমরাও হয়ে উঠেছি দক্ষিণ এশিয়ায় একটি আদর্শ ও অনুকরণীয় দেশ। সামাজিক সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় কেবল শ্রীলংকা ও ভারতের কেরালা রাজ্য আমাদের চেয়ে এখনো এগিয়ে। আর কেউ নয়। আসুন, আগামী বাজেটে আমরা কয়েকটি সহজ কাজে অর্থ বরাদ্দ দিই। জবাবদিহি ব্যবস্থা তৈরি করি। তাহলে স্বাস্থ্য খাতে অনেক চাপ কমে যাবে। ফলে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুভয় থাকবে না। লক্ষ্য হবে আগামী এক বছরে আমাদের কার্যক্রমে ঈর্ষণীয় গতির সৃষ্টি করা। দেখবেন কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে, দেশের নানা রোগের প্রকোপ কমবে। স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য হবে।
ড. এ. কে. এনামুল হক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট